
ককবরক কাব্যচর্চার বর্তমান হালচাল
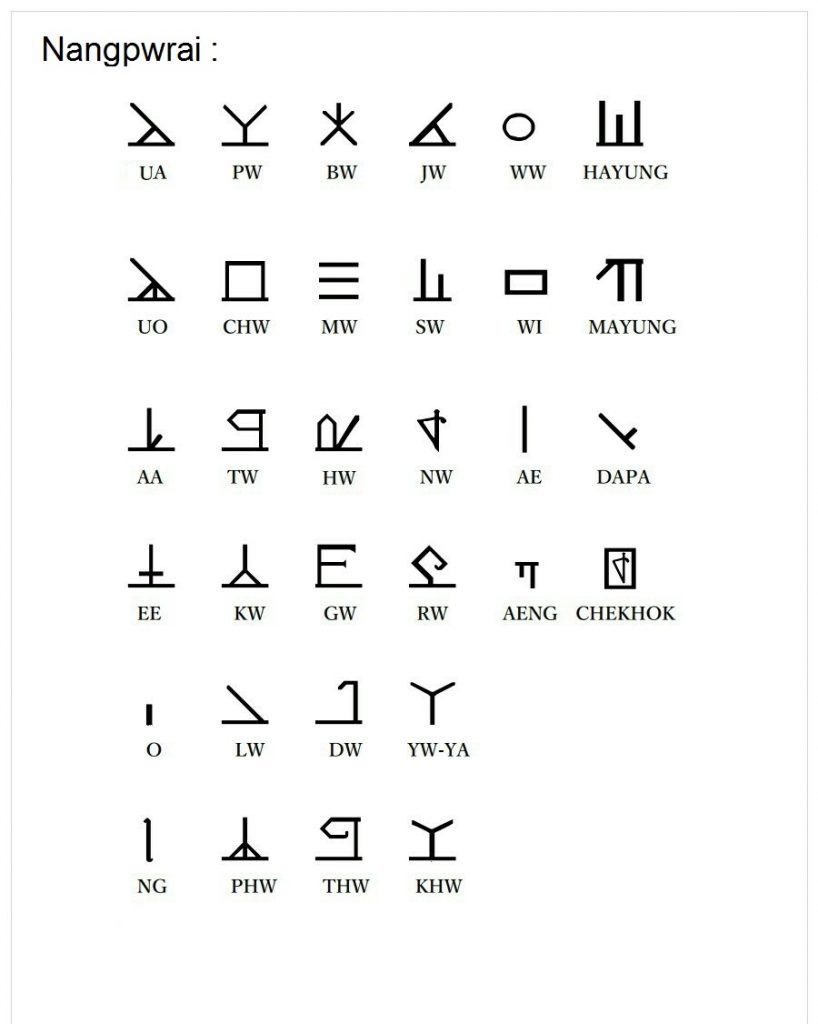
পরিশ্রান্ত সময়ে সমবেত আহারে ব্যস্ত ত্রিপুরা জুমিয়া লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি পাঠান-মিজোদের আনাগোনা দেখে সহজে সতর্কবাণী ফুটে ওঠে গায়েন কবিদের মুখে। চারিদিকে গোলাগুলিতে ত্রস্ত গ্রামবাসী, অসহায় নারী ও শিশু। তা-ই দেখে গায়েন কবি ব্যাকুল হয়ে গেয়ে উঠেন।
হাপং খিকরক মাইবিদি দুরুম দারাম-ন খানাদি পাথান ফাইমানি নুংয়াদই? সইন্য ফাইমানি নুংয়াদই? সইন্য সং কাইসা থাংপাইয়ই লাম’ পেসোয়া রগইদং।সাহিত্যের আদিরূপ কাব্য-ছন্দ। উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, ‘অনেকে মনে করেন কবিতা একটি অপার্থিব দিব্য বস্তু এবং তাকে আয়ত্ব করবার জন্যে মুনিঋষিদের মতো, নির্জন পাহাড়ে-পর্বতে কিংবা বনে-জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করতে হয়। আমি তা মনে করি না।
আমার বিশ্বাস, জাতে যদিও আলাদা তবু কবিতাও সাংসারিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের এই সাংসারিক জীবনের মধ্যেই তার বিস্তর উপাদান ছড়িয়ে পড়ে আছে।’
দুনিয়ার বড়ো বড়ো কবিতার সৃষ্টি হয়েছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের হাত ধরে। বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ হিসেবে পূজিত চর্যাপদ-ও ছন্দোময় গানের সংকলন ছিল।
কবিতা লেখা বিশেষ কোন শ্রেণির মানুষের জন্য কেউ নির্ধারণ করে দেয়নি। এখানেও নীরন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘কবি হবার জন্যে লম্বা-লম্বা চুল রাখবার দরকার নেই।
সর্বক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার নেই। কখন চাঁদ উঠবে, কিংবা মলয় সমীর বইবে, তার প্রতীক্ষায় থাকবার দরকার নেই।
ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি পরবার দরকার নেই।’ কারণ, ছোট চুল রেখে, খাতা-কলমের দিকে তাকিয়ে, দিনের আলোয় বা ঘোর অন্ধকার রাতে হারিকেন বা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে, রীতিমত জিন্সপ্যান্ট আর টাইট শার্ট পরিধান করে অথবা উদোম গায়েও কবিতা লেখা যায়।
কবিতা এমনতর একটি সাধারণ সাংসারিক বস্তু। অবশ্যম্ভাবীরূপে ককবরক সাহিত্যও যাত্রা শুরু করে কাব্য-ছন্দোময় পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে।
আদিকাল হতে ১৯০০ সালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ককবরক সাহিত্য আলো-আঁধারি পথ পাড়ি দিয়েছে। এই সময়কালে নানা সাহিত্যের কথা লোক মুখে শোনা গেলেও কেউ নির্দ্দিষ্ট করে কোন প্রমাণ হাজির করাতে পারেননি।
নানা লোকগীতি ও পূজা অর্চ্চনার বিষয়াদি এই সময়কালে সংকলিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে খুব কম অথবা প্রচার ও প্রসার ঘটেছে খুব কম।
বহু গীতিকাব্য ও উপাখ্যান রচিত হয়েছে এই সময়কালে যার সবক’টিই ছিল লোকমুখে প্রচলিত।
পুন্দা তান্নাই, কুচুক হা সিকাম কামানি, খুম কামানি, গাঁ তলিঅ থাঁমানি ইত্যাদি গীতি উপাখ্যান লোকমুখে প্রচলিত ও লোকমানসে নন্দিত ককবরক লোকসাহিত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম।
১৯০০ সালের পর কিছু সাহিত্য অন্ধকার ভেদ করে আলোর কাছাকাছি আসতে শুরু করে। এই সময়কালে মূলত অভিধান, ব্যাকরণ, লোকগাঁথা সংকলন, গানের সংকলন ইত্যাদি সাহিত্য কর্ম দেখা যায়।
এই সময়কালে ককবরক লিখিত সাহিত্যের সূর্যোদয়ের যুগে ককবরকের ছোট্ট বীজ অঙ্কুরিত হয়ে তার শাখা প্রশাখা প্রসারিত করতে থাকে।
ধর্ম থেকে রাজনীতি, সমাজ থেকে রাষ্ট্র, ছড়া থেকে উপন্যাস, অনুবাদ থেকে মহাকাব্য সকল বিষয় ককবরক সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে উঠতে থাকে এই পর্বে।
বাংলাদেশের ককবরকভাষি মানুষেরা এই সময়কালে নানা গীত-সংগীত সংকলনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এখানকার লেখালেখির প্রথম প্রকাশিত নিদর্শন হিসেবে উনিশশত চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে সাধক খুশীকৃষ্ণ ত্রিপুরা কর্তৃক রচিত ককবরক আধ্যাত্মিক সংগীত-এর কথা উল্লেখ করা যায়।
তাঁর লেখা ৩৩ টি আধ্যাত্মিক ককবরক সংগীত নিয়ে ১৯৪২ সালে ‘ত্রিপুরা খা-কাচাংমা খুম্বার বই’ নামের এই গানের বইটি প্রকাশিত হয়।
এই গানের বইটিকে বাংলাদেশে ককবরকের লিখিতরূপের সূচনালগ্ন হিসেবে গণ্য করা যায়। এরপর থেকে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেকেই ককবরকে লেখালেখি চর্চা করতে থাকেন।
ত্রিপুরা জাতির সাধু ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ককবরক চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন বহুদিন আগে থেকে।
আশির দশকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরাদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বৈসু উপলক্ষে নানা সাময়িকী প্রকাশ করতে থাকে। যা স্বল্প পরিসরে হলেও নিজের ভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত ককবরক কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বরেন ত্রিপুরা, মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, ব্রজনাথ রোয়াজা প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।
আশির দশকটি ছিল ককবরক লিখিত সাহিত্যের জোয়ারপর্ব। এই সময় সৃষ্টির জোয়ারে যেন উত্তাল হয়ে ওঠে ককবরক সাহিত্য জগত।
বাংলাদেশের কবিতা লিখিয়েদের তালিকায় যোগ হতে থাকে নতুন নতুন নাম। প্রভাংশু ত্রিপুরা, প্রশান্ত ত্রিপুরা, কাবেরী ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রনাথ রোয়াজা, প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা, দীনময় রোয়াজা, লাল দেনদাক, চিরঞ্জীব ত্রিপুরা, সুরেশ ত্রিপুরা, মঞ্জুলাল ত্রিপুরা, কুহেলিকা ত্রিপুরা, রঘুনাথ ত্রিপুরা, উল্কা ত্রিপুরা, শ্রাণী রোয়াজা, দীপক ত্রিপুরা, সুনীতি রঞ্জন ত্রিপুরা, অনিল চন্দ্র ত্রিপুরা, মায়াদেবী ত্রিপুরা, কৃষ্ণ ত্রিপুরা, হিরন্ময় রোয়াজা এই সময়কালের সক্রিয় কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
উল্লেখিত নামগুলোর মধ্যে অধিকাংশের নামই এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। এই নামগুলোর মধ্যে কেবল প্রভাংশু ত্রিপুরা, প্রশান্ত ত্রিপুরা ও দীনময় রোয়াজার লেখালেখি এখনও আমরা দেখি।
এই দশকে সাহিত্য সৃষ্টির প্রবল জোয়ার-ভাটায় পরিশোধিত হয়ে ককবরক যেন আধুনিক যুগের অথৈ সরোবরে অবগাহনের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।
এই পর্বকে ককবরকের বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবেও ধরে নেওয়া যেতে পারে। ককবরক সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখা এই সময়ে আরো পরিক্কতা লাভ করতে থাকে।
১৯৯১ সালে ‘সান্তুআ’ নামের একটি সাহিত্য সাময়িকী প্রশান্ত ত্রিপুরার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম এই সাহিত্য পত্রিকা পরবর্তীতে ‘সান্তুআ জার্নাল’ নামে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।
এই সাহিত্য পত্রিকা সৃষ্টির পর কবিতা লেখালেখিতে সংযোজিত আরো কিছু নতুন নাম। সালকামৗং ত্রিপুরা, গীতা দেববর্মন, অপুল ত্রিপুরা, ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, রত্না বৈষ্ণব, মন্ত্রজয় ত্রিপুরা, বিদ্যুৎ শংকর ত্রিপুরা, খুমুই ত্রিপুরা, হরিপূর্ন ত্রিপুরা, দয়ানন্দ ত্রিপুরা, প্রতিভা ত্রিপুরা, তর্ক কুমার ত্রিপুরা, তপন ত্রিপুরা, লিপিকা ত্রিপুরা, পিপিকা ত্রিপুরা, বিনয় কুমার ত্রিপুরা, সৃজনী ত্রিপুরা, প্রিয়াংকা পুতুল প্রমুখের কবিতা এই সময়কালের বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হয়। সান্তুআ জার্নালে লেখালেখি না করলের বি,এল, ত্রিপুরা (বরেন) এই সময়ের সক্রিয় একজন কবি।
অন্যদিকে ককবরকে সরাসরি না লিখলেও ত্রিপুরা লোকসমাজের নানা উপাদান নিয়ে রচিত কবিতার জন্য বেশ জনপ্রিয় একজন কবি শোভা ত্রিপুরা।
সাম্প্রতিক আমার বন্ধু কবি বি,এল ত্রিপুরা (বরেন) একটি দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ফেইসবুক স্ট্যাটাস লিখেছেন, ভাবছি বাংলাদেশে ককবরক সাহিত্যের উন্মেষ আদৌ ঘটবে কিনা! আমার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বলছে, ‘না’। আপনার মতামত কী? এই স্ট্যাটাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকে নানা অভিমত দিয়েছেন।
অনেকে বলেছেন, এই সাহিত্যের অবশ্যই উন্মেষ ঘটবে। তাঁর স্ট্যাটাস ব্যাখ্যা হিসেবে মন্তব্য কলামে বন্ধুবর বরেন লিখেন, আমি চারটি বই লিখেছি, তার মধ্যে দুইটি ককবরক-বাংলা দ্বিভাষিক, কিন্তু সাড়া তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়।
ফেইসবুকে অনেক ‘লাইক’ পেয়েছি। কিন্তু বইগুলো কিনেছেন খুব কমসংখ্যক মানুষ। এই যাবৎ মাত্র দুইজন ক্রয়ের আগ্রহ দেখিয়ে ফোন করেছেন।
বাকি সবাই সৌজন্য কপি পেতে ইচ্ছুক। ছোটদের জন্য লেখা ককবরক ছড়ার বইটি বাংলাদেশের ককবরকভাষিদের জন্য প্রথম অভিজ্ঞতা হলেও আশানুরূপ তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি।
বরেন ত্রিপুরার এই স্ট্যাটাসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ককবরক সাহিত্যের বর্তমান চিত্র উঠে এসেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ না হলে এই দেশে ককবরক কবিতা বা সাহিত্যের বিকাশ অপ্রস্ফুটিতই থেকে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।
তাই বরেন ত্রিপুরার স্ট্যাটাসের মন্তব্যে সক্রিয় ও জনপ্রিয় ফেইসবুকার কবি প্রশান্ত ত্রিপুরার লেখা কথা এখানে প্রনিধানযোগ্য, ককবরক সাহিত্যের বর্তমান দৈন্যদশা নিয়ে সকলেরই ভাবা উচিত।
আমার কথা হলো, ককবরক সাহিত্য নিজ থেকেই প্রস্ফুটিত হবে না। আমরা ককবরকভাষিরা যদি মনে প্রাণে চাই তবে তা অবশ্যই প্রস্ফুটিত হতে বাধ্য।
কিন্তু কথা হলো তা কিভাবে প্রস্ফুটিত হবে, সেটিই হলো ধর্তব্য। আমরা যদি চেষ্টা অব্যাহত রাখি, তাহলে সময়োপযোগি সুন্দর সাহিত্যের প্রস্ফুটন একদিন ঘটবেই।
বরেন ত্রিপুরার দীর্ঘশ্বাস যেন সুদুর ঢাকা থেকে পার্বত্য জনপদে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমরা প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ করে বৈসুকে কেন্দ্র করে নানা সাময়িকী প্রকাশ করি।
কোন কোন নবীন কবি তার লেখা কবিতার প্রথম প্রকাশ দেখে হয়তো উদ্বেলিত হয়। আরো নতুন নতুন কবিতা সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে।
তাদের মধ্য হতে হয়তো বা নব্বই শতাংশই হারিয়ে যাবে কালের গর্ভে। যে ক’জন টিকে থাকবে, তারাও হয়তো আমাদের প্রজন্মের মতো করে ফেইসবুক, ট্ইুটারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ট্যাটাস দেবে। আবারও সেমিনার হবে, হবে আলোচনা।
অতি উৎসাহী কোন কবির প্রকাশিত বই অবহেলায় পড়ে থাকবে ঘরের সবচেয়ে অন্ধকারময় কোণে। ইঁদুর আর উইপোকার খাদ্যে পরিণত হবে সেসব বই।
আমরা কি আমাদের কাব্যচর্চার এই দশা দেখতে চাই? নিশ্চয়ই চাই না। তাহলে উপায় কী? আসুন জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিনিয়ত চর্চা করে যাই আমাদের সাহিত্যকর্ম।
নিজে লিখবো, অন্যকেও লিখতে উৎসাহিত করবো। নিজে কিনবো, অন্যকেও কিনতে উৎসাহিত করবো। কারণ বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।
তথ্যঋণ:
নন্দ লাল শর্মা, সাহিত্য জগতে ত্রিপুরাদের ভূমিকা, পুব-ই-রাবাইনি সাল, ত্রিপুরা উপজাতি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংসদ, ১৯৮১। হিমেল বরকত (সম্পা), বাংলাদেশের আদিবাসী কাব্যসংগ্রহ, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৩। সান্তুআ জার্নালের বিজয় দিবস ও অন্যান্য সংখ্যা।আরও কিছু লেখা


